বাংলা ভাষার সংকট ও সম্ভাবনা (Crises and Potentials of Bengali Language)
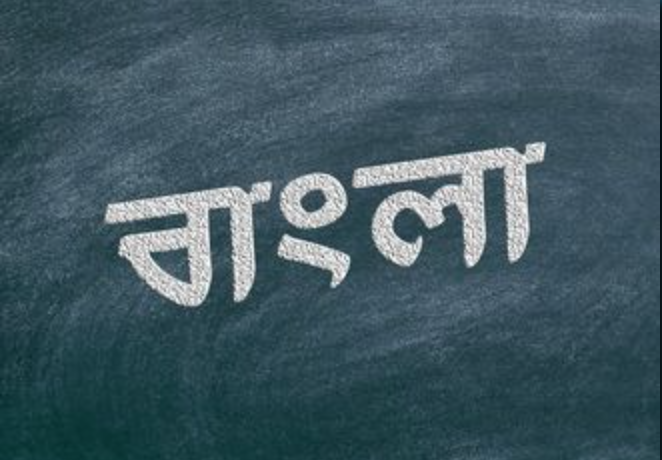
গত দুই দশকে নতুন এক বাস্তবতায় প্রবেশ করেছে বাংলা ভাষা। নতুন প্রজন্মসহ দেশের প্রায় সব বয়সী মানুষই কোনো না কোনোভাবে প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠেছে। দিনে দিনে অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইংরেজির চেয়েও বাংলা অনেক বেশি ব্যবহূত হচ্ছে।গত ২ ফেব্রুয়ারি ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বিশ্বে ফেসবুক ব্যবহারে এখন তৃতীয় স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্বশিক্ষিত মানুষও এখন ব্যবহার করছে এ সামাজিক যোগাযোগ। ফলে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা কতটা ব্যবহার উপযোগী হয়েছে।
একবিংশ শতকের প্রথম দশকের শেষদিকে ফেব্রুয়ারি মাসগুলোতে বাংলা ভাষার নতুন এক সমস্যার কথা বলা হতে লাগলো: ‘ভাষাদূষণ। নতুন প্রজন্মের একটি অংশ ইংরেজি ঢঙে এবং অন্য একটি অংশ আঞ্চলিক ঢঙে বাংলা শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করছে। বাংলা বলার সময় বাংলা শব্দের পরিবর্তে তারা ইংরেজি, হিন্দি ও আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করছে। বাংলাভাষার ‘করুণ অবস্থা’ নিরসনকল্পে ১৯শে ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যালামনাই এ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব রকিবুদ্দিন আহমেদ।
আদালত তাঁর আবেদন আমলে নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের একাধিক মন্ত্রণালয় ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের উপর রুল জারি করেছিলেন। আমি মনে করি,বাংলা ভাষার দূষণ আসলে রজ্জুতে সর্প দর্শনের মতোই একটি মতিভ্রম। দূষণ নিয়ে হৈচৈ আসলে বাংলা ভাষার প্রকৃত সমস্যাকে আড়াল করে এর দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি করছে এবং পরিণামে বাংলাভাষী জনগণের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে শ্লথ করে দিচ্ছে।
কমপক্ষে দু’টি উচ্চারণভঙ্গী প্রমিত বাংলার বিকৃতি ঘটাচ্ছে
কমপক্ষে দু’টি উচ্চারণভঙ্গী প্রমিত বাংলার বিকৃতি ঘটাচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়: ১. ইংরেজি উচ্চারণ ভঙ্গি ও ২. আঞ্চলিক উচ্চারণভঙ্গি। এফ. এম. রেডিওর সঞ্চালক, (উচ্চ) মধ্যবিত্ত পরিবারের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়া ছেলেমেয়েদের কথায় ইংরেজি উচ্চারণভঙ্গী লক্ষ্য করা যেতে পারে। বাংলাদেশের বেশির ভাগ লোকের প্রমিত ভাষা ব্যবহারে আঞ্চলিক উচ্চারণভঙ্গি লক্ষ্য করা যাবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই দুই উচ্চারণভঙ্গীর কারণে প্রমিত বাংলার উচ্চারণভঙ্গী বদলে যাবার কোনো সম্ভাবনা আদৌ আছে কিনা।এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের জানতে হবে, কমবেশি ত্রিশ কোটি বাংলাভাষীর মধ্যে কত কোটি মানুষের মাতৃভাষা প্রমিত বাংলা?
বেশির ভাগ বাঙালি প্রমিত বাংলা বুঝতে পারেÑ এটা যদি ধরেও নিই, সবাই নিশ্চয়ই প্রমিত বাংলা বলতে সক্ষম নন। কত কোটি মানুষ প্রমিত বাংলা আদৌ বলতে পারেন? কত কোটি মানুষ কোনো বিশেষ টান ছাড়া প্রমিত বাংলা বলতে পারেন? কত কোটি মানুষ শিক্ষিত? শিক্ষিত বাঙালিরা ছাড়া অন্যরা কি প্রমিত বাংলা বলতে পারেন? এই পরিসংখ্যানগুলো না পেলে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না, প্রমিত বাংলার উচ্চারণ আদৌ কোনো ঝুঁকির মধ্যে আছে কিনা।
বাংলা ভাষা ব্যবহারে সংকট কোথায়
বাংলা ভাষা ব্যবহারে উদাসীনতা কেন- এ প্রশ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ঔপনিবেশিক মানসিকতার জন্য ইংরেজির ব্যবহার হচ্ছে। আর তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ব্যবহারের জন্য কারিগরি সমস্যা দায়ী। সাধারণ মানুষ যিনি বাংলা-ইংরেজি দুই-ই জানেন, তিনিও ইংরেজিতে লিখে থাকেন। এর জন্য দায়ী বাংলার নানা ফন্ট। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি ফন্ট হওয়া উচিত।
এ জন্য একটি কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে। তারা বিদ্যমান ফন্টগুলো পর্যালোচনা করে ঠিক করবে কোনটি সুবিধাজনক, সেটাই ব্যবহারের জন্য স্বীকৃতি পাবে। এই ফন্ট আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন মেনে করতে হবে। যাতে বিশ্বজনীন হয়। তাঁর মতে, বর্তমানে একেকজন একেক ফন্ট ব্যবহার করায় ফন্টগুলো ভেঙে যায়, অনেক মাধ্যমে তা দেখাও যায় না। এই সংকট বাংলা ভাষা ব্যবহারে অন্যতম প্রধান অন্তরায়।
ভাষা-সংকট ও ভাবনা-দৈন্যের কথা
বর্তমানকালের ‘বিশ্বপথিকদের’ আতিশয্যে দেশে ইংরেজিয়ানার জোয়ার চলছে। এ নিয়ে কারও দুর্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না, কারণ, সংস্কৃতির অগ্রজনেরাও গড্ডলিকায় গা ভাসিয়েছেন। কেউ ভাবছেন না যথাযথ বয়সে মাতৃভাষায় যথাযথ সাহিত্যপাঠ না করলে বড় হয়ে কেউই আর আপন সংস্কৃতির অন্দরের মানুষ হতে পারেন না। অন্য ভাষাভাষীদের মধ্যে দু-চারজন একাগ্র নিষ্ঠায় আবু সায়ীদ আইয়ুব বা ফাদার দ্যতিয়েন হতে পারেন, কিন্তু সে তো ব্যতিক্রম।
এ কথাটাও বলা দরকার, শৈশব থেকে ঠিকভাবে শেখানো হলে শিশুর পক্ষে দুটি, এমনকি তিনটি ভাষা শেখাও কঠিন নয়। তারা তো গণিত শিখছে, যা উচ্চতর জ্ঞানচর্চার ভাষা বা বাহন বৈ আর কি! ফলে বাংলায় জোর দিলে ইংরেজি শেখা হবে না, এমন ধারণা ভুল। কিন্তু মাতৃভাষার সাহিত্য শৈশব থেকে পাঠ করে বড় না হলে শিশুর জীবনে সাংস্কৃতিক বৃক্ষটির ডানা কাটা পড়বে কিংবা মূল শিকড় বাদ যাবে—হয় সে ফুলে-ফলে বিকশিত হবে না, নয়তো বামন হয়ে অকেজো হয়ে থাকবে। তার পক্ষে মানবজীবনের চরিতার্থতা খোঁজার পথ খোলা থাকবে না।
সাহিত্যপাঠ দিয়েই একজন শিক্ষিত মানুষ উচ্চতর ভাবের বিষয়ে পঠনপাঠনের জন্য তৈরি হয়। এ অংশ বাদ গেলে একজন মানুষ বেশি হলে সরল ও স্বাভাবিক মানুষ হতে পারে (ম্যাথু আর্নল্ডের ভাষায় simple and natural), কিন্তু মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ (noble and grand) হতে পারে না। অথচ এ পথেই চিন্তার গভীরতায় পৌঁছাতে পারে মানুষ। শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা যদি এ পথ খুলে দিতে না পারে, তবে মানুষ হয়ে জন্মানোর আনন্দ ও সার্থকতার বোধ হারিয়ে যাবে। খেয়ে-পরে চলে সঙ্গসুখে বা কামে-ক্রোধে-হর্ষে, পুলকে-ক্রন্দনে বাঁধা যে জীবন, তার উত্তেজনা ও চরিতার্থতার বোধ ক্ষণিকের এবং তা অপ্রাপ্তির আফসোস ও পরবর্তী প্রাপ্তির কামনায় নিরন্তর অস্থিরতায় ভোগাতে থাকে। সেটাকেই মানবজীবনের নিয়তি ভেবে নেওয়া চরম ভুল হবে।
বাংলা ভাষার নব সম্ভাবনা
একুশ আসে সম্ভাবনার দুয়ার খুলে। এই সম্ভাবনার আরও দুয়ার খুলে দেবে যদি বাংলাদেশ ইউএনএলের (ইউনিভার্সাল নেটওয়ার্কিং ল্যাঙ্গুয়েজ) সদস্যভুক্ত হয়। বর্তমানে ইউএনএলভুক্ত ভাষার সদস্য সংখ্যা ১৬৫। কিন্তু বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ ভাষা বাংলা এখনো এর সদস্যপদ নিতে পারেনি। এই সদস্যপদ নেওয়ার জন্য কিছু পূর্ব প্রস্তুতি প্রয়োজন। যেমনÑ ইউএনএল নির্মিত ছকে বাংলা ভাষার একটি ডিজিটাল অভিধান ও একটি ডিজিটাল শব্দকোষ তৈরি করা। ইউএনএলের পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সাল নেটওয়ার্কিং ল্যাঙ্গুয়েজ ফাউন্ডেশন, জেনেভা।
বিশ্বের প্রতিটি ভাষা যেন ইউএনএলের সুবিধা নিতে পারে এবং প্রত্যেক মানুষ যেন অবাধে এর ব্যবহার করতে পারে, সে জন্য ইউএনএল বিনামূল্যে খুলে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ বাংলাকে এই প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি করার উদ্যোগ নিয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় অবকাঠামো ও আর্থিক সহযোগিতা দিয়েছে।
ভাষার ব্যবহার হয়ে যাবে বহুমাত্রিক
প্রযুক্তিবিদ ও ভাষাবিদদের সমন্বয়ে একদল গবেষক ও কলাকুশলি ইউএনএল প্রযুক্তির সঙ্গে কাজ করতে পারে এমন একটি ডিজিটাল শব্দকোষ ও অভিধান নির্মাণে কাজ করে যাচ্ছেন। গবেষকরা মনে করেন, রবীন্দ্রসাহিত্য অভিধান তৈরি ও ভাষা নির্মাণে একটা বড় ভূমিকা রাখবে। এশিয়াটিক সোসাইটির এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কলকাতার এসএনএলটিআর। আশা করা যায়, দেশী-বিদেশী গবেষকদের চেষ্টায় স্বল্প সময়ের মধ্যে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। বাংলাভাষাও ইউএনএলের সদস্যভুক্ত হয়ে এ প্রযুক্তি ব্যবহারের অনুমোদন পাবে। তাতে বাংলা ভাষার ব্যবহার হয়ে যাবে বহুমাত্রিক।
বিশ্বের যে কোনো দেশের যে কোনো প্রান্তের যে কোনো বাংলাভাষাী মানুষ একটি মাত্র বোতাম টিপে অন্য ভাষাকে যেমন নিজের ভাষায় পড়তে পারবে, ঠিক তেমনি অন্য ভাষার মানুষও বাংলা ভাষার রসাস্বাদন করতে পারবে নিজের ভাষায়। এর জন্য বিদেশী ভাষা শেখার দরকার হবে না। ডিজিটাল বাংলা বিশ্বকে নিয়ে আসবে হাতের মুঠোয়। খুলে দেবে সম্ভাবনার নব দুয়ার। বাংলা ভাষা যদি তার স্বকীয়তা, বৈশিষ্ট্য, মাধুর্য ও উৎকর্ষ বজায় রেখে ইউএনএলের সদস্যভুক্ত হয়ে শিল্পে, সাহিত্যে, ব্যবসায় বাণিজ্যে স্থান করে নিতে পারে, তবে তা হবে বাংলা ভাষার নবদিগন্তের নবযাত্রা।
ডিজিটাল জগতে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাড়াতে আরও পদক্ষেপ নিতে হবে
একুশে ফেব্রুয়ারিই পারে বাংলা ভাষাকে এগিয়ে যাওয়ার সেই উদ্দীপনা দিতে। ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে হলে ভাষাবিদদের পাশাপাশি রাষ্ট্র এবং প্রযুক্তিবিদদেরও সক্রিয় হতে হবে। মায়ের ভাষায় প্রযুক্তি ব্যবহার করেই দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। আমাদের ইতিবাচক দিক হচ্ছে প্রযুক্তিমনস্ক সরকার ক্ষমতায়। প্রযুক্তির ব্যবহার করে বাংলা ভাষায় লেখাপড়া ও চর্চা এবং ভাষাকে টেকসই করায় বিশেষজ্ঞ জ্ঞান থেকে উৎসারিত সরকারি কিছু উদ্যোগ নিতে হবে।
ডিজিটাল জগতে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাড়াতে কাজ করতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্পের আওতায় সফটওয়্যার ও টুলসের ব্যবহার শুরু হলে তা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে বাংলা ভাষাকে বৈশ্বিকীকরণের সুযোগ সৃষ্টি করবে। ডিজিটাল ডিভাইসে আরও ভালোভাবে এবং সহজে বাংলা ভাষায় লেখাপড়া ও অনুবাদ সহজ হবে।
বাংলা ভাষার উন্নতির সম্ভাবনা ও অন্তরায়
বাংলা ভাষায় রেনেসাঁসের স্পিরিট তখনো ক্রিয়াশীল ছিল। সরকারি প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ওই প্রতিটি আন্দোলনই ছিল বাংলা ভাষার, বাংলা সাহিত্যের ও বাংলা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য প্রেরণাদায়ক। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে আমাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ উন্নতির ধারায় চলবে, এটা সবাই আশা করেছিল। এই সময়ে বাংলা ভাষার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়েও শিক্ষিত সমাজে অভূতপূর্ব আশা দেখা দিয়েছিল।
একজন লেখকের লেখায় দেখছি : ‘বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার, লালন করার এবং তাকে অন্তহীন শুভ পরিণামের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলার পূর্ণ দায়িত্ব বাংলাদেশরই। এ ধারণাটি এখন ব্যক্তিগত, শ্রেণিগত ও সম্প্রদায়গত চেতনাকে অতিক্রম করে রাষ্ট্রগত ও জাতিগত চেতনায় এসে সুস্থির হয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। দেশের স্বাধীনতা ও মানুষের মুক্তিকে যাঁরা পরম কাঙ্ক্ষিত বিষয় বলে উপলব্ধি করেন, বাংলা ভাষার সাফল্যে তাঁদের সংশয় নেই।’
প্রচলিত শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার অপরিহার্য
জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনে শিক্ষা খাতে সব রকম বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য পরিহার করতে হবে। প্রচলিত শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার অপরিহার্য। প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যসূচি, পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উন্নত করতে হবে। কথিত সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতির জায়গায় অনুসন্ধিৎসামুখী, জ্ঞানমুখী পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে। ইংলিশ ভার্সন বিলুপ্ত করতে হবে।
বাংলাদেশে বিদেশি সরকার কর্তৃক পরিচালিত সব স্কুল বন্ধ করতে হবে। মাদরাসা শিক্ষা নিয়ে বিতর্ক এড়িয়ে চলতে হবে। সর্বজনীন কল্যাণে মূলধারার বাংলা মাধ্যমের শিক্ষাকে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দিয়ে উন্নত করতে হবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। অনেকে বিশ্বমান অর্জনের কথা বলেন। তাঁরা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী কর্মনীতি নির্বিচারে অনুসরণ করার কথা বলেন। এটা ঠিক নয়। উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ও নীতি-বিধি সংস্কার করতে হবে। চলমান শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে জাতি ও রাষ্ট্র গড়ে উঠছে না, উঠবে না।
সমাজে বাংলা চর্চা ও বাংলা ভাষার অবস্থান
সাহিত্য সৃষ্টির প্রশ্নে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ-ত্রিপুরা স্বস্তিকর অবস্থায় আছে, এমনটা আমরা ধরে নিতে পারি। কিন্তু ভাষার সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবহারের দিকে ফিরে তাকালে একাধিক কারণে শঙ্কা ও ভয় দেখা দেবে বৈকি। বিশেষ করে যদি সে মাতৃভাষার সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক, জীবিকার সম্পর্ক না থাকে। যদি সেখানে বিদেশি ভাষা, বিজাতীয় ভাষা শক্তিশালী অবস্থান পাকা করে নেয়।
এ সমস্যা ভাষিক জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের ও সেটা অনেকের চোখে স্ববিরোধিতার এক বিস্ময়কর উদাহরণ। কিন্তু সে সমস্যা ভারতীয় ইউনিয়নের প্রান্তিক রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে অধিকতর, যেখানে বাঙালি শিক্ষিত সমাজে ইংরেজি ও হিন্দির আগ্রাসন এত ব্যাপক যে তাদের মাতৃভাষা বাংলা পিছু হটতে হটতে দুয়োরানির চেয়েও খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছে। সে পশ্চাৎগতি অব্যাহত, সেখানেই যত সমস্যা।তাই সেখানকার একটি সাহিত্য পত্রিকার ঐক্যতান ২-এর প্রচ্ছদপত্রে লেখা হয়েছে, 'আক্রান্ত মাতৃভাষা, আসুন প্রতিরোধ করি'।
বাংলায় বিদেশি ভাষার সংমিশ্রণ: সমাধান কোন পথে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, 'সংরক্ষণবাদী দৃষ্টি, বিদেশি শব্দ ব্যবহার করাই যাবে না বা বাংলা বাক্যের মধ্যে যদি বিদেশি শব্দ থাকে তাহলে অনেক বড় ধরনের বিপদ হয়ে যাবে, এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। কিছু বিদেশি শব্দ আছে যেগুলো অভিধান ঘাটলে হয়তো একটা বাংলা শব্দ তৈরি করা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ওই বাংলা শব্দ ব্যবহারকারীদের কাছে গৃহীত হবে কি না। এই চ্যালেঞ্জ কিন্তু সবসময় থাকবে। এক্ষেত্রে প্রাঞ্জল, খুব যুতসই বাংলা হওয়া প্রয়োজন। ভাষা ব্যবহারকারীদের মনস্তত্ব, চিন্তাভাবনা, তাদের সুবিধা-অসুবিধা এসব চিন্তা করতে হবে।'
'আবার টেকনিক্যাল ওয়ার্ল্ডে এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলোর বাংলা করলে ওইসব শব্দের সঙ্গে এক ধরনের দূরত্ব তৈরি হবে। পৃথিবী এখন বেঁচেই আছে মূলত প্রযুক্তির ছত্রছায়ায়। তাই বাংলা পরিভাষা তৈরির নামে যদি কঠিন, দুর্বোধ্য নতুন শব্দ তৈরি হয় তাহলে দেখা যাবে প্রযুক্তির থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। এটা ভীষণ আত্মঘাতী চিন্তা হবে। যেমন: জোর করে কম্পিউটারের বাংলা তৈরি করার কোনো প্রয়োজন নেই।'
তথ্যসুত্র
দুর্বোধ্য নতুন শব্দ তৈরি হয় , The Daily Star.
ভাষার বিলুপ্তি , Kalerkantho.
সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, Kalerkantho.
বাংলা ভাষার সমস্যা , Shishirbhattacharja.
ভাষাবিদদের পাশাপাশি রাষ্ট্র, Banglanews24.
বাঙালিরা জীবন উৎসর্গ করেছে, Dailyjanakantha.
বিশ্বভাষা তালিকায় বাংলার অবস্থান পঞ্চম।, Samakal.
প্রভাব পড়ছে ভাষার ওপর, Prothomalo.