বাংলাদেশের সাহিত্যের সম্ভাবনা (Potential of Bangladesh Literature)
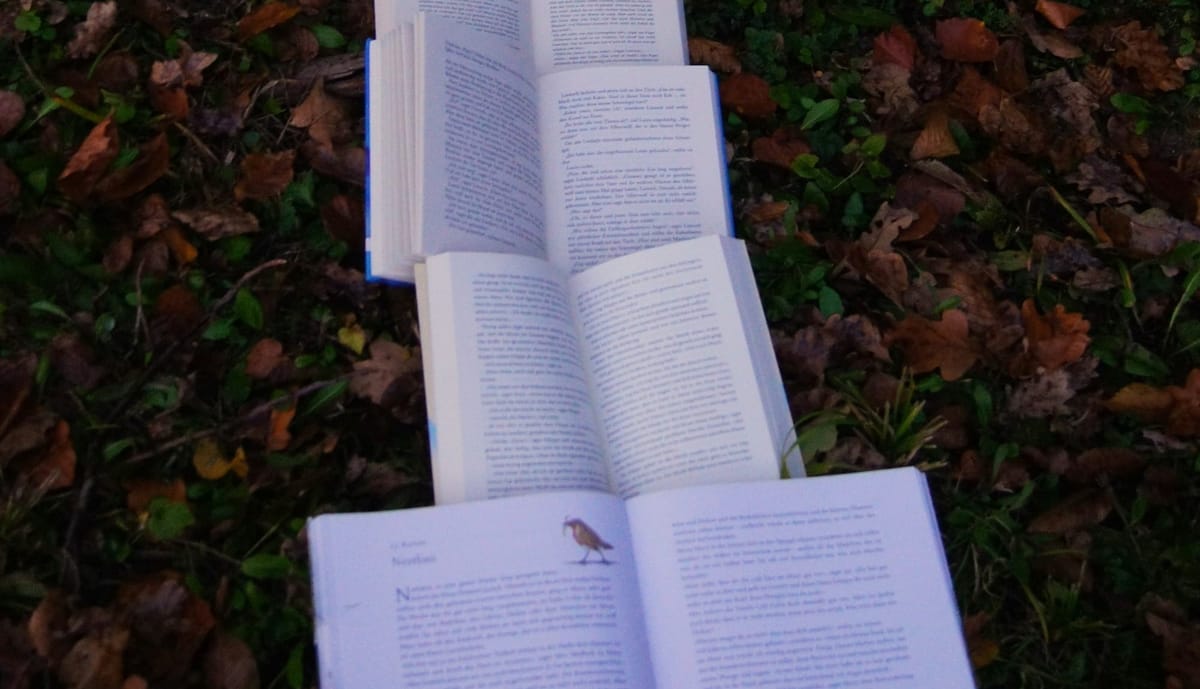
বৈশ্বিক জ্ঞান সূচকের (গ্লোবাল নলেজ ইনডেক্স) তালিকায় বিশ্বের ১৩৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১২তম। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিচে বাংলাদেশ। আমরা জানি জ্ঞানই জীবনপ্রদীপ। জ্ঞান দ্বারাই লিখিত ও পঠিত হয় সাহিত্য। এ কারণে আমাদের জনসংখ্যা বেশি হলেও পাঠক সংখ্য কম। কিন্তু পাঠক সংখ্যা কম হলেও অন্যান্য ভাষার তুলানায় লেখক সংখ্যা কম নয়। বেশি বেশি লেখক সংখ্যার যেমন ভালো দিকও আছে তেমন মন্দ দিকও আছে। মন্দ দিক হলো প্রচুর পরিমাণ মানহীন বই প্রকাশিত হলে পাঠক বিভ্রান্ত হয়ে সাহিত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাই এই দিকটি এখন নতুন প্রজন্মকে গভীরভাবে ভাবতে হবে।
সবচেয়ে আশাবাদী হওয়ার মতো বিষয় হচ্ছে, চীনা ভাষায় রবীন্দ্র রচনাবলির ৩৩ খণ্ডের অনুবাদ থেকে শুরু করে লালনের গান ও দর্শন ইংরেজি ও জাপানি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সোভিয়েত আমলে রুশ ভাষায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের ব্যাপক অংশের অনুবাদ হয়েছে।সাম্প্রতিক এ ধারা অব্যাহত থাকায় গবেষকরা মনে করছেন, ইংরেজি, চীনা ও জাপানি ভাষার পর বাংলা ভাষা নিয়ে বিশ্বের আগ্রহ যেমন বাড়ছে, তেমনি এ ভাষার প্রসার ও চর্চা বেড়ে চলেছে।
বাংলা সাহিত্য : সংকট ও সম্ভাবনা
বর্তমানে সাহিত্যের অন্যতম প্রধান একটি সংকট হলো—পাঠক সংকট। সংকট বইয়েরও আছে; তবে সেটা পরিমাণের নয়, মানের। অবশ্য ‘মানের’ সংকটটি গৌণ হয়ে উঠছে এই কারণে যে, কিছু ভালো বইও তো হচ্ছে, তার পাঠক কই? থাকলে, তা কতজন? কথা আসতে পারে—সাহিত্যের পাঠক কারা? বই পড়ার মতো শিক্ষা ও পাঠের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে যার, তিনিই পাঠক। শৈশব-কৈশোরে দেখেছি, আমার বাবার মতো কিছু দূর লেখাপড়া জানা লোকেরা চাকরিবাকরি না করলেও হাতের কাছে বই পেলেই সেটা পড়তেন বা নাড়াচাড়া করে দেখতেন, সেটা ধর্মপুস্তকই হোক আর পঞ্জিকাই হোক।
বাংলাদেশের সাহিত্য : পঞ্চাশ পেরিয়ে
দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর জুড়ে বাংলাদেশের সাহিত্যকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। বাঙালির জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ও তাত্ত্বিক পটভূমিতে কেবলই পূর্ব বাংলার বাঙালিকে সম্পৃক্ত করে নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশের সাহিত্যের বয়ান। এ কারণে বাঙালির বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক সৃষ্টশীলতাকে মূল উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণের সমস্যা এই যে, বাংলাদেশের বহুভাষিক, বহুসাংস্কৃতিক ও বহুজাতিক বাস্তবতা এখানে হারিয়ে যায়। কেননা বাংলাদেশ কেবল বাঙালির রাষ্ট্র নয়; অপরাপর অনেক ভাষাভাষী জাতি ও জনগোষ্ঠী বহু বছর ধরে এদেশে বসবাস করছে; অপর ভাষার সৃষ্টিশীলতা বাংলাদেশের সাহিত্য স্বাগত জানায়নি।
বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরের সাহিত্যে হুমায়ূন এক বিরাট বিস্ময়
বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরের সাহিত্যে হুমায়ূন এক বিরাট বিস্ময়। গল্প বলার অসাধারণ ক্ষমতা তার ছিল। রম্য, রহস্য, কল্পবিজ্ঞান, ইতিহাস, সমকাল তার রচনার বিষয়। বিচিত্র কৌশল ও বিষয়ের সমাবেশ এক লেখকের ভেতর পাওয়া দুর্লভ ঘটনা। তাই তার জনপ্রিয়তার মিথ ও বাস্তবতাকে কেউ কেউ নতুন করে খুঁড়ে দেখতে উদ্যোগী হয়েছেন।জাতিগত পরিচয়ের মানদণ্ডে বাংলাদেশ সব সময়ই বহুজাতিক। একভাষিকতার বাইরে গিয়ে প্রসারিত চোখে আমাদের তাকাতে হবে চাকমা, মারমা, গারো, সাঁওতাল, মণিপুরি, উর্দু ভাষার সাহিত্যে। একইসঙ্গে একই সঙ্গে আলোচনার পরিকাঠামোতে আনতে হবে ইংরেজি ভাষায় রচিত সাহিত্যকে। হয়তো তখনই রচিত হবে বাংলাদেশের সাহিত্যের সত্যিকার সমবায়ী ইতিহাস। পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসের মহাবয়ানকে সাজাতে হবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বয়ানের সমাবেশে।
বর্তমান সাহিত্য পরিস্থিতি ও দেখন-সাহিত্য
ক্ষমতাকেন্দ্রিকতা ও পশ্চিমের চিন্তাদর্শনের সঙ্গে গভীর সংযুক্তির বিষয়গুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এর বিষয় ও প্রকরণ, ভাষা ও শৈলীকে পাল্টে দিয়ে উত্তরাধুনিক সাহিত্য একটা বিকল্প উপহার দিচ্ছে। আমাদের সমাজেও কেন্দ্রিকতা, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি বাড়ছে, পুঁজি অতি আগ্রাসী হচ্ছে। হয়তো এসবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য সাহিত্য যখন এগিয়ে আসে, তখন অপ্রথাগত চিন্তা, অপরিচিত ভঙ্গি, কাঠামো ও ভাষা হবে এসব পরাস্ত করার একটা কার্যকর উপায়। তবে স্বীকার করতেই হবে, এই সময়ে দৃশ্যমাধ্যম ও ডিজিটাল প্রযুক্তির কারণে (এবং এদের মাধ্যমে) সাহিত্যের একটি নতুন ঢেউয়ের যে সৃষ্টি হয়েছে, তার নিবন্ধগুলোও ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে।
দেখন-সাহিত্যের যেটুকু আদল এখানে দেখা যাচ্ছে, তা প্রধানত লেখকদের এই ভাবনাকে ধারণ করে যে তাঁদের এবং তাঁদের বইকে পাঠকের দৃষ্টিগোচর করতে হবে। বিজ্ঞাপন সব সময় সেই কাজটি করে, প্রচারও। ফেব্রুয়ারি মাসে পত্রপত্রিকা ও এগুলোর সাহিত্য পাতাজুড়ে বইয়ের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, তার একটি উদ্দেশ্য বইয়ের সঙ্গে লেখককে পাঠকের দৃষ্টিতে স্থান দেওয়া।
সাহিত্যের ভাষা, শৈলীগত বিভিন্ন প্রয়োগকৌশলে দৃশ্যের অনুভবটি মূর্তমান
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখকেরা আরও খোলাখুলিভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। যিনি করেন না, তিনি প্রান্তে থেকে যান। যিনি যত বেশি করেন, তিনি তত পাঠকের দৃষ্টিতে থাকেন। তবে এসবের বাইরেও দেখন-সাহিত্যের একটি পরিচয় এর অন্তর্গত দৃশ্যমনস্কতা (যাকে ইংরেজিতে ‘ভিজ্যুয়ালিটি’ বলা যায়)। অনেক পাঠক এখন দেখতে চান, দেখাটা তাঁদের কাছে পড়াকে ছাড়িয়ে যায়, তা ছাড়া সাহিত্যের ভাষা, শৈলীগত বিভিন্ন প্রয়োগকৌশলে দৃশ্যের অনুভবটি মূর্তমান।
সমকালীন বাংলা সাহিত্য-চর্চার সমস্যা ও সম্ভাবনা
আভিধানিকভাবে ‘সহিতের ভাব’ বা ‘মিলন’ অর্থে ‘সাহিত্য’ হলো কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি সৃজনশিল্পের মাধ্যমে এক হৃদয়ের সঙ্গে অন্য হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন; সাহিত্য¯্রষ্টা-সাহিত্যের সাথে পাঠকের এক সানুরাগ বিনিময়। কিন্তু আভিধানিক অর্থের নির্দিষ্ট সীমায় সাহিত্যের স্বরূপ-গতি-প্রকৃতি-বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতির সম্যক ধারণা দেওয়া যেমন অসম্ভব, কোনো বিশেষ সংজ্ঞায় তাকে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়াও তেমন দুঃসাধ্য।
বাচ্যার্থ ও ব্যঞ্জনার্থর সীমাকে অতিক্রম করে নানা রূপে
বাচ্যার্থ ও ব্যঞ্জনার্থর সীমাকে অতিক্রম করে নানা রূপে, রসে, প্রকরণ ও শৈলীতে সাহিত্যের নিরন্তর যাত্রা সীমা থেকে অসীমে। প্রত্যক্ষ সমাজপরিবেশ তথা সমকালীন বাস্তব পারিপার্শ্বিক, নিসর্গপ্রীতি ও মহাবিশ্বলোকের বৃহৎ-উদার পরিসরে ব্যক্তিচৈতন্য ও কল্পনার অন্বেষণ ও মুক্তি- আর এইভাবেই শ্রেণিবিভাজন, নামকরণ ও স্বরূপমীমাংসার প্রচেষ্টাকে ছাপিয়ে উঠে সাহিত্যের যাত্রা সীমাহীনতায়। প্রকৃত সাহিত্য তাই যেমন তার সমসময় যা যুগমুহূর্তের, তেমনই তা সর্বকালের সর্বজনের।
সাহিত্যের মৌল উপকরণসামগ্রী আহৃত হয়
মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্বে বাস্তব সমাজজীবনকে ‘ভিত্তি’ আর শিল্প-সাহিত্যকে সমাজের উপরিকাঠামোর [ঝঁঢ়বৎংঃৎঁপঃঁৎব] অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। সাহিত্যের মৌল উপকরণসামগ্রী আহৃত হয় জীবনের ভা-ার থেকে- সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বৈরিতার বিচিত্র-অনিঃশেষ ভা-ার থেকে। সাহিত্যসৃষ্টির মূলে সক্রিয় যে সৃজনী-ব্যক্তিত্ব তা নিছক বিমূর্ত কোনো সত্তা নয়; আত্মপ্রকাশ ও মানবিক সংযোগ ও বিনিময়ের বাসনায় অনুপ্রাণিত সে সত্তা তার ভাব-ভাবনা, বোধ ও বিশ্বাসকে এক আশ্চর্য কৌশলে প্রকাশ করে জনসমক্ষে কোনো একটি বিশেষ রূপ-রীতি-নীতির আশ্রয়ে।
ব্যক্তিক অনুুভূতি-যাপিতজীবন-মিশ্রকল্পনার জগৎ থেকেই সৃষ্টি হয় সাহিত্যের; যুগান্তরের আলোকবর্তিকা হিসেবে সাহিত্য সত্যের পথে সবসময় মাথা উঁচু করে থেকেছে- সত্যকে সন্ধান করেছে। আসলে সাহিত্য এমনি এক দর্পণ- যাতে প্রতিবিম্বিত হয় মানবজীবন, জীবনের চলচ্ছবি, পরিবেশ-প্রতিবেশ, সমাজজীবনে ঘটমান ইতিহাস- ইতিহাসের চোরাস্রােত নানাবিধ কৌণিক সূক্ষ্মতায়।
“সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে অনেকে ভাবতে শুরু করেছেন
আসলেই যে-কথাই বলিনা কেন সাহিত্যিকও মানুষ- সমাজের বাসিন্দা- সমাজের নানান কর্মে তিনিও নিবিড়ভাবে জড়িত। সাহিত্যসৃষ্টি তো ঘরের কোনো এক খিল দেওয়া কামরায় সৃষ্টি হয়না- তাই সমাজের বৃহত্তর জীবন-জীবনের উর্বর-অনুর্বর ভূমি, ঘটনাপ্রবাহ সাহিত্যিকের পক্ষেও এড়িয়ে চলা অসম্ভব। কিন্তু সমস্যা হয় তখনই- যখনই সে নিজেকে কোনো একটি বৃত্তবন্দি কামরায়- ‘লাল-নীল-সাদা-কালো-গোলাপি’ মতাদর্শে নিজেকে বন্দি করেন। “সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে অনেকে ভাবতে শুরু করেছেন।
ভাবনা রীতিমত দুর্ভাবনার পর্যায়ে পৌঁছেছে
আজ সে-ভাবনা রীতিমত দুর্ভাবনার পর্যায়ে পৌঁছেছে, কারণ এক প্রবল রাজনৈতিক ধারা সাহিত্যকে আপন ঘূর্ণাবতের মধ্যে টেনে আত্মসাৎ করতে উদ্যত, যেমন করে মধ্যযুগে ধর্ম আত্মসাৎ করেছিল শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র বিকাশকে।” [আবু সয়ীদ আইয়ুব, ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক] এ-কথা সত্য যে দলীয় রাজনীতির প্রবেশ সাহিত্যের নির্মল সত্তাকে আবিল করে। সাহিত্যিক যতক্ষণ সাহিত্যকর্মরত ততক্ষণ তিনি একমাত্র নিজের প্রতিভারই অনুগামী, অন্য কোনো অধিনায়কের প্রত্যাদেশ মেনে চললে তিনি স্বধর্মচ্যুত হবেন- লক্ষ্যভ্রষ্ট হবেন। সাহিত্যিক সমাজের একজন বলে সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ করা তাঁর কর্তব্য এবং সাহিত্যিক বলেই সৌন্দর্যের আরাধনা করা তাঁর ধর্ম; এ দুটির সমন্বয় সাধিত হলে প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টির হয়- এর বিপরীত হলে এপাশ ওপাশ করতে গিয়ে লেখক ‘ধপাশ’ করে পড়েন।
বাংলায় বিশ্ব, বিশ্বে বাংলা: পঞ্চম বিশ্ব বাংলা সাহিত্য সমাবেশ’
প্রবাসে বাংলা সাহিত্যচর্চার এক অভূতপূর্ব মঞ্চ ‘উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য পরিষদ’ তাদের বার্ষিক ‘বিশ্ব বাংলা সাহিত্য সমাবেশ’ এবার আয়োজন করে কানাডার অন্টারিও প্রদেশের টরন্টোতে। ২০১৯-এ শুরু হওয়া এ বার্ষিক সমাবেশ এ নিয়ে তৃতীয়বার অনুষ্ঠিত হলো সাহিত্যিক-সাহিত্যামোদীদের সশরীর উপস্থিতিতে। আগের দুবার ছিল যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টা মহানগরীতে ২০১৯-এ গল্পকার ও অনুবাদক শাহাব আহমেদের নেতৃত্বে এবং ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের লেক ফরেস্ট শহরে ২০২২-এ কল্পবিজ্ঞান লেখক দীপেন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে।
সাহিত্য এবারের পঞ্চম সমাবেশে
মাঝে দুবার করোনা অতিমারির সময়ে আন্তর্জালে সমাবেশ করতে হয়েছিল। সশরীর সমাবেশের ক্ষেত্রে নির্বাচিত শহরটির তরফ থেকে একটি স্থানীয় আয়োজক দল বা সংস্থা এ কর্মযজ্ঞের মূল দায়ভার বহন করে থাকে। এবার সেই দায়িত্বে ছিল টরন্টোর ‘পাঠশালা’র, যা কিনা অনেক বছর ধরে শিল্প-সাহিত্যচর্চার এক প্রবাহমান প্ল্যাটফর্ম হিসেবে টরন্টো তথা বিশ্বের বঙ্গসমাজকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। অনুবাদক, পাঠশালার কর্ণধার ও সাহিত্য পরিষদের কর্মী ফারহানা আজিম শিউলী এবারের পঞ্চম সমাবেশের আহ্বায়ক। তাঁর নেতৃত্বে এই গুরুদায়িত্ব পালনে ‘পাঠশালা’কে সর্বতোভাবে, একনিষ্ঠভাবে ও সার্বক্ষণিকভাবে সাহায্য করেছেন ক্যালিফোর্নিয়ার স্যাক্রামেন্টো-নিবাসী, সাহিত্য পরিষদের কর্মী মোহাম্মদ ইরফান। আর তাঁদের পাশে থেকে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছেন ঔকভিলের হিল্লোল ভট্টাচার্য, শিকাগোর শৈবাল তালুকদার, ক্লিভল্যান্ডের সুজয় দত্ত, ফ্লোরিডার পূরবী বসুসহ সাহিত্য পরিষদের কয়েকজন অভিজ্ঞ সদস্য।
সাহিত্য সমালোচনা ও সমালোচনা সাহিত্য
সাহিত্য সমালোচনার একটা ইতিহাস তো আছে, ধ্রুপদী ধারা থেকে শুরু করে আজকের নতুন ধারার সমালোচনা পর্যন্ত একটা ছকে ফেলে যে কেউ সাহিত্য সমালোচনার একটা ধারাবাহিক প্রতিকৃতি তৈরি করতে পারবেন। আরিস্ততল-এর 'পোয়েটিকস' (খ্রীস্টপূর্ব ৪ শতাব্দী) বা তার সমসাময়িক ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্র' কে যথাক্রমে কবিতার আর ভারতীয় সংস্কৃত নাটকের আদি সমালোচনা (ফরমাল) ধরে রেঁনেসা (ফ্রান্সিস বেকন এবং তৎসমুদয়), অ্যানলাইটেনমেন্ট (ডেভিড হিউম, কান্ট, মেরি উলস্টোনক্রাফট এবং তৎসমুদয়), ঊনবিংশ শতাব্দীর সমালোচনা (হেগেল, মার্ক্স, নিটশে, জন স্টুয়ার্ট মিল, তলস্তয় এবং তৎসমুদয়), নব্য সমালোচনা (ফ্রয়েড, স্যস্যুর, ইয়াকবসন, সার্ত্র, সিমন দ্য ব্যোভয়াঁ, দেরিদা, ফুকো, বার্থ, লাকাঁ, দেলুজ, বাখতিন, ফ্রেই, চমস্কি, সাইদ এবং তৎসমুদয়) থেকে এই প্রতিকৃতি বর্তমানের এক বিমূর্ত-প্রয়োগবাদী-ভাষার-আন্তর্জাতিকরণী-দর্শনাশ্রয়ী সমালোচনার পর্দায় ফেলে আলোচনা করা সম্ভব।
বিজ্ঞানের দর্শন, দর্শনেরও বিজ্ঞান জন্ম নিয়েছে
সাহিত্য বলি, দর্শন বলি বিজ্ঞানমনস্কতা না নিয়ে কোনোটাই আগাতে পারে নি, বা বলা যায় বিজ্ঞানের দর্শন, দর্শনেরও বিজ্ঞান জন্ম নিয়েছে। পশ্চিমের বেলায় তা আরো বেশি প্রযোজ্য। আরিস্ততল-এর 'পোয়েটিকস' আর ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্র' পাশাপাশি রেখে কি এক ধরনের তুল্য-বিচার করা যায়? যদিও 'পোয়েটিকস' সরাসরি সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হলেও 'নাট্যশাস্ত্র' বরং পারফরমিং আর্টসের সঙ্গে যুক্ত, তবু এক শাখার শিল্পবিচারের সঙ্গে অন্য শাখার কোথাও কোথাও মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। যেমন 'নাট্যশাস্ত্রে'র অন্তর্গত সংগীত, নৃত্য আর অভিনয়কলার নন্দনতত্ত্ব বহুলাংশে কবিতার নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অন্যদিকে এই দুই প্রাচীন সমালোচনা তত্ত্বের টেক্সট বা আদিপাঠকে নানাভাবে পাশাপাশি রেখে আলোচনা, বিশ্লেষণ করে দেখা যায়।
সাহিত্য কি বা কোনো কিছু আদৌ সাহিত্য হয়ে উঠলো
সাহিত্য কি বা কোনো কিছু আদৌ সাহিত্য হয়ে উঠলো কি না এই বিচারের পদ্ধতি, সাহিত্যের উপাদান যেমন–গঠন, শৈলী, নান্দনিকতা, বিষয়, দর্শন, ভাষা, এরকম নানা রকমের উপাদানের ভূমিকা, কখনও কখনও একটি উপাদানের ওপরে অন্যগুলোর বা অন্যটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তো সাহিত্যতত্ত্বের নানান শাখা প্রশাখাও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এ যুগে, অন্তত পশ্চিমা বিশ্বে সমালোচনা সাহিত্য মূলত সাহিত্যতত্ত্বের বা দর্শনের আলোচনাকেই নির্দেশ করে। এজন্য একটু পশ্চিমা ধারাগুলোকে ধারাবাহিকভাবে খতিয়ে দেখলে আমার নিজস্ব চিন্তার প্রবাহটাকে পাঠকের কাছে তুলে ধরতে সুবিধা হবে।
তথ্যসুত্র
বাংলাদেশে সাহিত্য সমালোচনা , Bangla.BD News24.
এক বিশেষ ভাষাভাষী অভিবাসী সম্প্রদায়, Nagorik.Prothomalo.
সাহিত্য হচ্ছে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, Onnodristy.
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিকল্প বুদ্ধিমত্তা হিসেবে আবির্ভূত হবে, Prothomalo.
সাহিত্যকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে, Dhakapost.
বাংল সাহিত্য কি বিরাট কোনো সংকটের মুখোমুখি?, Songbadprokash.
বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কী? , Dainikbangla.